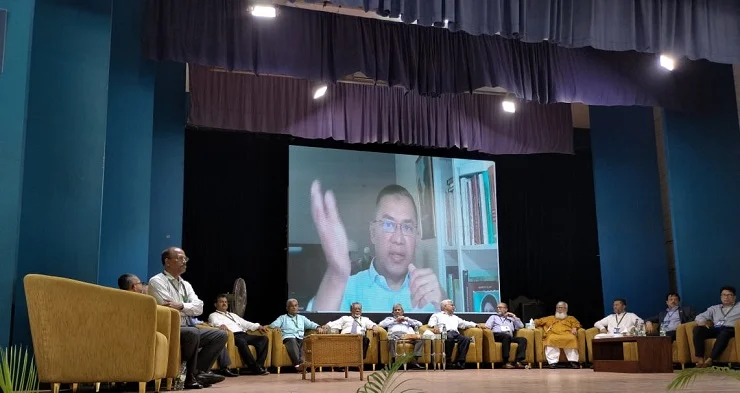জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
দুই মেয়াদের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না, এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, দুই মেয়াদে দশ বছর; এটাতে ঐকমত্য আছে। এটা তো বিএনপির প্রস্তাবনা, যা আট বছর আগে বিএনপি দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তার আগে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বিএনপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যারা এখন নতুনভাবে সংস্কারের কথা বলছে, তারা এখন এই কথা বলছে। আমরা ভিশন ২০৩০-এর মধ্যেই বলেছি দুই মেয়াদের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। এখানে ঐকমত্য না থাকার কোনো কারণ নেই।
মাইকেল মিলারের সঙ্গে বৈঠকের আলোচনার বিষয় জানতে চাইলে আমির খসরু বলেন, সবার আগে নির্বাচন। এটা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসে হতে যাচ্ছে, এজন্য সবার একটা প্রস্তুতি আছে, সন্তুষ্টি আছে। তারা আশা করছেন, আমরা দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ ফিরে যাবে। তারা তো সবাই অপেক্ষা করছেন একটি নির্বাচিত সরকারের ওপর, তাদের কর্মকাণ্ড কী হবে তা দেখার জন্য। এতে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় আছে, যেগুলো একটি নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে করতে সবাই স্বস্তি বোধ করবে। এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।
তিনি বলেন, আপনারা জানেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে। আমাদের দেশে শ্রমিকদের যে সমস্যা আছে এবং তাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা জানতে চেয়েছেন আমাদের চিন্তাভাবনা কী। আগামী দিনের পার্লামেন্টকে তারা সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনা করার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে।